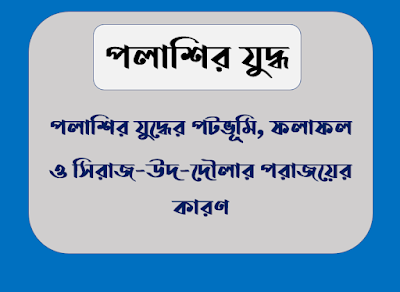পলাশির যুদ্ধের পটভূমি
ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক উন্নয়নঃ
সূচনা:
১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আলীবর্দী খান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি সফলভাবে রাজ্য শাসন করেছেন। সুকৌশলে ইংরেজ বণিক কোম্পানিকেও নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর বাংলার রাজনীতিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার পর থেকে তাকে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। তিনি সফলভাবে পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র 'দমন করলেও তার বিরুদ্ধে বাইরের ষড়যন্ত্রের আরেক জাল বিস্তৃত হতে থাকে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশি যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করতে থাকে।
পলাশি যুদ্ধের পটভূমির বর্ণনা:
সিরাজ-উদ-দৌলার সিংহাসনে বসার মধ্য দিয়েই পলাশির যুদ্ধের পটভূমিকা রচিত হওয়া শুরু হয়।আর তার সমাপ্তি ঘটে ১৭৫৭ সাল চূড়ান্ত যুদ্ধের মাধ্যমে। নিম্নে পলাশি যুদ্ধের পটভূমি আলোচনা করা হলোঃ
উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব:
নবাব আলীবর্দীর মৃত্যুর আগে তার কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে বাংলার সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। ১৭৫৬ খ্রিঃ আলীবর্দীর মৃত্যু হলে তার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা ২২ বছর বয়সে নবাবের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সিংহাসনে বসার পর থেকেই উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে। বিশেষ করে আলীবর্দী খানের তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘোষেটি বেগম সিরাজের নবাব হওয়ায় আশাহত হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।
এদের সঙ্গে যোগ দেন ঘোষেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সিরাজের খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ এবং অন্যান্যরা। কৌশলে নবাব ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দি রাখেন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে সিরাজ-উদ-দৌলা এক যুদ্ধে তাকে পরাজিত ও নিহত করে পূর্ণিয়া দখল করে নেন। আপাতত দ্বন্দ্বের নিরসন হলেও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং পলাশি যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হতে থাকে।
নবাবের প্রতি আনুগত্যহীনতা :
সিরাজ-উদ-দৌলা যখন বাংলার নবাব হন তখন মুঘল ভারতের প্রচলিত প্রথা অনুসারে ফরাসি, ডাচ কোম্পানি এবং বাংলার জমিদাররা নতুন নবাবকে উপহার উপঢৌকন দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে এবং নবাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তা না করে নবাবের মর্যাদাহানি করে। তারা নবাবের প্রতি কোনোরূপ সম্মান প্রদর্শন না করে চরম আনুগত্যহীনতার পরিচয় দেয়। এই ঘটনা নবাবকে ইংরেজদের প্রতি চরমভাবে ক্রদ্ধ করে।
কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদান :
জাহাঙ্গীর নগরের দিউয়ান রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সরকারি কোষাগার থেকে ৫৩ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে পরিবার পরিজনসহ ইংরেজ কোম্পানির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিরাজ কৃষ্ণদাসকে তার হাতে অর্পণ করার জন্য কলকাতার ইংরেজ গভর্নর ড্রেককে নির্দেশ দেন। কিন্তু ড্রেক নবাবের আদেশ অমান্য করেন। ফলে সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যকার সম্পর্ক আরো বৈরি হতে থাকে।
দুর্গ নির্মাণ সংক্রান্ত জটিলতা:
নবাব আলীবর্দী খান ইউরোপীয় বণিকদেরকে তার রাজ্যে দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি দেননি। আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের আশঙ্কায় নবাবের বিনা অনুমতিতে ইংরেজ ও ফরাসিরা চন্দনগরে দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করে। নবাব অবিলম্বে ইংরেজ ও ফরাসিদের দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করার এবং নির্মিত অংশ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। ফরাসিরা নবাবের আদেশ মানলেও কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাবের আদেশ অমান্য করেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নতুনভাবে নির্মাণ করে আরো দুর্ভেদ্য করে তোলে। এই ঘটনা নবাবের সার্বভৌমত্বকে হেয় করে। যা পরবর্তীকালে পলাশি যুদ্ধের পটভূমিকা রচনায় সহায়তা করে।
দত্তক সংক্রান্ত জটিলতা:
মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ার ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে এক ফরমান দ্বারা ইংরেজ কোম্পানিকে বিনা শুে সমগ্র ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অধিকার প্রদান করেন। বিনাশুল্কে আমদানি-রপ্তানির সুবিধার জন্য কোম্পানিকে যে ছাড়পত্র দেওয়া হয় তা দত্তক নামে পরিচিত। বিনা শুল্কে সমগ্র ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার বিনিময়ে কোম্পানি মুঘল সরকারকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।
কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা শীঘ্রই দত্তকের অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। মুর্শিদকুলি খান ইংরেজদের ফরমান লাভের মধ্যে অশুভ সংকেত লক্ষ করে এর বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, কোম্পানি তার রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য শুল্ক ছাড়পত্র বা দস্তক ভোগ করলেও কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য দস্তক ব্যবহার করবে না।
কিন্তু সিরাজ ক্ষমতাসীন হয়ে লক্ষ করলেন, কোম্পানির কর্মচারীরা শর্ত অমান্য করে ব্যক্তিগত ব্যবসা করছে এবং নবাবকে কর ফাঁকি দিচ্ছে। এর ফলে নবাবের রাজকোষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। নবাব ইংরেজ গভর্নর ড্রেককে দত্তকের অপব্যবহার বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ড্রেক তা অগ্রাহ্য করেন। এর ফলে নবাব ইংরেজদের প্রতি ভীষণভাবে ক্ষুদ্ধ হন।
কলকাতা দখল :
১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজ মুর্শিদাবাদ থেকে সসৈন্যে শওকত জঙ্গকে দমন করার উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হন। ২০ মে তিনি যখন রাজমহলে পৌঁছান তখন গভর্নর ড্রেক প্রদত্ত পত্র তার হস্তগত হয়। এই পত্রে ড্রেক ইংরেজদের সদিচ্ছার কথা প্রতি নম্র ভাষায় সিরাজকে জানালেও দুর্গ নির্মাণ বন্ধ কিনা সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেননি।
এতে ক্রুদ্ধ হয়ে নবাব পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর না হয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতার ইংরেজগণকে উপযুক্ত শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করে কলকাতার দিকে অগ্রসর হন। ১৬ জুন সিরাজ কলকাতার উপকণ্ঠে পৌছান। কলকাতা দুর্গের সৈন্য সংখ্যা খুব অল্প ছিল।
কলকাতাস্থ ইংরেজ ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়াম দখল করতে সিরাজকে বেগ পেতে হয়নি। গভর্নর ড্রেক ও অপরাপর ইংরেজগণ ফোর্ট উইলিয়াম ত্যাগ করে জলপথে ফলতা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২০ জুন কলকাতার নতুন গভর্নর হলোওয়েল আত্মসমর্পণ করেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলকাতার দুর্গে প্রবেশ করেন।
ইংরেজ কর্তৃক কলকাতা পুনঃদখল :
কলকাতা হাতছাড়া হবার পর ইংরেজ কোম্পানি মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভের অধীনে একদল সৈন্য ও এডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে এক নৌবহর কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠান। ক্লাইভ ও ওয়াটসন বিনা বাধায় কলকাতা উদ্বাস্তু ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর ইংরেজ সৈন্য ও নৌবহর কলকাতার দিকে যাত্রা করে।
নবাবের বজবজে একটি ও তার কাছেই আরো একটি দুর্গ ছিল। মানিকচাঁদ এই দুর্গ দুটি রক্ষার্থে অগ্রসর হচ্ছিলেন- পথে ক্লাইভের সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ফলে মানিকচাঁদ পলায়ন করে। ইংরেজরা বজবজ দুর্গ ধ্বংস করে এবং বিনা যুদ্ধে কলকাতা অধিকার করে। এরপর তারা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সুরক্ষিত করে।
নবাব কর্তৃক ২য় বার কলকাতা আক্রমণ :
কলকাতা অধিকার করেই ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অপরদিকে নবাব সিরাজও কলকাতা অধিকারের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। ক্লাইড ১০ জানুয়ারি হুগলি অধিকার করে শহরটি লুণ্ঠন করেন এবং পার্শ্ববর্তী বহু গ্রাম পুড়িয়ে দেন। ১৯ জানুয়ারি নবাব হুগলি পৌঁছালে ইংরেজরা কলকাতায় প্রস্থান করেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি নবাব কলকাতার শহরতলীতে আমীর চাঁদের বাগানে শিবির স্থাপন করেন।
৫ ফেব্রুয়ারি শেষ রাতে ক্লাইভ ও ওয়াটসন অকাম্মাৎ নবাবের শিবির আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণের ফলে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০০ লোক নিহত হয়। কিন্তু সকালে নবাবের সৈন্য সুসজ্জিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ করলে ক্লাইভ প্রস্থান করেন। কলকাতা জয় করার মত নবাবের যথেষ্ট সৈন্য সংখ্যা ছিল। কিন্তু তারপরও নবাব ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে যুদ্ধ না করে ইংরেজদের সাথে আলীনগরের সন্ধি স্থাপন করেন।
ইংরেজ কর্তৃক ফরাসিদের পরাজয় :
আলীনগরের সন্ধি ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। সেই সুযোগে ইংরেজরা তাদের অপর শত্রু ফরাসিদের পরাজিত করতে বদ্ধপরিকর হয়। ফরাসিদের সাথে সিরাজের ঐক্য যাতে স্থাপিত হতে না পারে ক্লাইভ প্রথমে সেই ব্যবস্থাই করতে চাইলেন। ইতোমধ্যে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল।
সেই সূত্র ধরে নবাবের আপত্তি সত্ত্বেও ক্লাইভ ফরাসি ঘাঁটি ও বাণিজ্য কেন্দ্র চন্দনগর অধিকার করে নেন। আহমদ শাহ আবদালিও এসময় দিল্লি অধিকার করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন করেছিলেন। পূর্ব ভারতের দিকে আবদালির অগ্রসরের সংবাদ প্রচারিত হলে সিরাজ অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। সুতরাং তিনি ইংরেজদের অসন্তুষ্ট করতে সাহসী হলেন না।ফলে ইংরেজদের হাতে বাংলাদেশে ফরাসিদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের সাহায্য প্রাপ্তির আশাও বিনষ্ট হলো।
কিন্তু পলাতক ফরাসিরা মুর্শিদাবাদে আশ্রয় পেলে ক্লাইভ প্রমাদ গোনলেন। সিরাজ দাক্ষিণাত্যে বুসীর সঙ্গে আলাপ প্রত্রালাপ করছেন এ সংবাদও ইংরেজদের অজানা রইল না। এরূপ পরিস্থিতিতে ইংরেজরা এটা বুঝতে পারলো যে, যতদিন সিরাজ সিংহাসনে আসীন থাকবেন ততদিন তাদের স্বার্থ নিরাপদ থাকবে না। নিজেদের মনোনীত কোনো লোককে মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত করতে পারলেই তাদের স্বার্থ নিরাপদ হবে এই ধারণা ইংরেজদের মনে বদ্ধমূল হলো।
নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র:
এই অবস্থায় মুর্শিদাবাদে সিরাজের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। সিরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে তদস্থলে মীরজাফরকে অধিষ্ঠিত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।
ষড়যন্ত্রকারীরা তৃতীয় পক্ষের সহায়তা লাভের জন্য ক্লাইভের নিকট এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করলে কলকাতার সিলেক্ট কমিটি ও ক্লাইভ আনন্দে ষড়যন্ত্রকারীগণকে সাহায্য করতে সম্মত হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ইংরেজ ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র রচিত হয়। যা পলাশির যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হবার মঞ্চ তৈরি করে ।
সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের কারণ
পলাশির যুদ্ধে নবাব বহুসংখ্যক নিয়েও অল্প সংখ্যক সৈন্যের ইংরেজ বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। পলাশির প্রান্তরে নবাবের পরাজয় এবং সিংহাসন থেকে বিতাড়নের পিছনে নানাবিধ কারণ ছিল। নিম্নে পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ আলোচনা করা হলো।
রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব :
মাতামহ আলীবর্দী খানের অত্যধিক স্নেহে লালিত পালিত সিরাজ-উদ-দৌলার মানসিক দৃঢ়তার বড় অভাব ছিল। তিনি ছিলেন হঠকারী এবং অস্থির স্বভাবের। একথা ঠিক যে, সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যে তিনি যেভাবে ঘসেটি বেগমের চক্রান্ত নস্যাৎ করে তাকে বন্দি করেন, পূর্ণিয়ার, শাসনকর্তা শওকত জঙ্গ এর বিদ্রোহ দমন এবং যুদ্ধে তাকে নিহত করেন এবং কলকাতা দখল করেন তা সত্যই উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে।
কিন্তু কলকাতা বিজয়ের পর তার এসব সাফলা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে কর্পূরের মতো উঠে যায়। কলকাতা দখল করে তার যথাযথ সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে তিনি মানিকচাদের ন্যায় দুর্নীতিপরায়ণ সেনানায়কের হাতে কলকাতার ভার অর্পণ করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যা তার পরাজয়ের পিছনে ইন্ধন যুগিয়েছিল।
মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা :
পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের জন্য প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাই প্রধানত দায়ী ছিল। নবাব মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা আগেই জানতে পেরেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে প্রধান সেনাপতির পদে বহাল রাখেন। আর মীরজাফরের কুপরামর্শে মোহনলালকে যুদ্ধক্ষেত্রে ত্যাগের এবং যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ফলে ক্লাইভের বাহিনী পিছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। এতে করে নবাবের বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যে কারণে যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ঘটে।
কূটনৈতিক অদূরদর্শিতা:
নবাব দ্বিতীয়বার কলকাতা অভিযানের সময় তার মনবল হারিয়ে ফেলেন। কলকাতা জয় করার মত নবাবের যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য থাকলেও তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে তাদের সঙ্গে অপমানজনক আলীনগরের সন্ধিতে আবদ্ধ হন । হয়তো নবাবের মনে তার সেনাধ্যক্ষদের বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। নবাব যদি তার অসৎ সেনাধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তাহলে তারা ভয় পেয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি তা না ফের অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। যা পরিণামে তার পতন ডেকে আনে।
অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা:
নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সিংহাসন লাভ করার প্রাক্কালে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ততটা ভালো ছিল না। তাই কারণে অকারণে তাকে অমাত্য ও জগৎশেঠের মতো বিত্তশালীদের দ্বারস্থ হতে হতো। এরূপ অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে নবাব দু'দুবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ফলে রাজকোষ আরো শূন্য হয়ে পড়ে। নবাব যদিও জগৎশেঠের চক্রান্ত বুঝতে পারেন কিন্তু আর্থিক বোঝার কারণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। এরূপ অর্থনৈতিক দুর্বলতাও তার পতনের জন্য দায়ী ছিল।
নৌশক্তির অভাব :
১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবের পতনের অপর কারণ ছিল তার নৌশক্তির অভাব। পক্ষান্তরে ইংরেজদের অধীনে ছিল শক্তিশালী নৌবহর। এই নৌবহরের সাহায্যেই ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলকাতা অধিকার করতে পেরেছিলেন। নবাবের শক্তিশালী নৌবহর থাকলে নবাবের পক্ষে ইংরেজ শক্তির মোকাবিলা করা সহজ হত। কিন্তু তা না। থাকায় নবাব সহজেই যুদ্ধে পরাজিত হন। ৬. ব্যক্তি স্বার্থের প্রভাব : অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাংলায় সর্বত্র চরিত্র সংকট দেখা দেয়। সংকীর্ণ মানসিকতা দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা বাঙালির চরিত্রকে কলুষিত করে তোলে।
ব্যক্তি স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে তখন কেউ কুণ্ঠিত হতেন না। সমাজে উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেই এই অবক্ষয়ের ছাপ বেশি দেখা যায়। অবশ্য ইংরেজরাও এ অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্ত ছিল। না। মীরজাফর, খাদিম হোসেন, মানিকচাঁদ, নন্দকুমার, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ প্রমুখ ব্যক্তি স্বার্থের জন্য বাংলার স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছিলেন।
প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের প্রভাব :
যুদ্ধে নবাবের আরেকটি কারণ ছিল প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের প্রভাব। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের পর পরই নবাব প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন। এই ষড়যন্ত্র জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যদি মীরজাফর, জগৎশেঠ এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের আটক করতেন তাহলে চক্রান্ত বেশিদূর এগোতে পারত না। কিন্তু নবাব সবকিছু সম্পর্কে অবহিত হয়েও মীরজাফরকেই প্রধান সেনাপতির পদে বহাল রাখেন। মীরজাফরকে বিশ্বাস করে নবাব মারাত্মক ভুল করেন। যার পরিণতি তার পতন।
যুদ্ধক্ষেত্রে মীরমদনের মৃত্যু :
পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের মৃত্যু। রিয়াজ-উস-সালাতনের লেখক বলেছেন, “নবাবের পক্ষেই জয়ের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কামানের গোলায় নবাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মীরমদন নিহত হলে, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।” ইংরেজ লেখক লিউক ক্র্যাফটন যিনি পলাশিতে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও লিখেছেন, “আমাদের মীরমদনকে হত্যা করার সৌভাগ্য হয়েছিল।” মীরমদনের মৃত্যুতে নবাবের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। যার পরিণতি যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ।
ফরাসি সাহায্যের অভাব :
ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করলেও ফরাসিরা সবসময় নবাবের প্রতি তাদের আনুগত্য দেখিয়েছে। কিন্তু নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সে আনুগত্যের মূল্য দিতে পারেননি। ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা ফরাসিদের চন্দনগর আক্রমণ করলে নবাব ফরাসিদের কোনো সাহায্য না করে মহা ভুল করেন। চন্দরনগরের পতনের ফলে বাংলায় ফরাসি শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষে নবাব ফরাসিদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হন। যার প্রভাব পলাশির যুদ্ধেও লক্ষ করা যায়।
নবাবের সামরিক দক্ষতার অভাব:
আলীবর্দী খানের অতিস্নেহে লালিত পালিত হওয়ার কারণে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মধে সামরিক, রণকৌশলগত কলাকৌশল ঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি। যার প্রমাণ পাওয়া যায় পলাশির যুদ্ধে তার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। সিরাজ-উদ দৌলার রণকৌশলগত দুর্বলতার কারণে তার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তার সামরিক বাহিনীর মধ্যে ঐক্যবোধের একান্ত অভাব ছিল। আর এজন্য বিশাল সৈন্যবাহিনীর পলাশির পান্তরে কেবল পরাজিত হয়নি, অযথা জীবন দেয়। নবাবের সৈন্যবাহিনীতে যদি ময়মনন ও মোহনলালের ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতির প্রতিফলন ঘটত তাহলে হয়তো বাংলার ইতিহাস অন্যখাতে প্রবাহিত হতো না ।
পলাশির যুদ্ধের ফলাফল
(ক) রাজনৈতিক ফলাফল :
২. পলাশির যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা কোম্পানির মর্যাদা লাভ করে।
(খ) অর্থনৈতিক ফলাফল
১. মীর জাফরের সাথে চুক্তি মোতাবেক পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা প্রচুর অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়। তাদের ব্যবসায় বাণিজ্য তখন সরগরমভাবে চলতে থাকে।(গ) সম্প্রদায়গত ফলাফল :
১. ভারতীয় মুসলমানগণ এতদিন প্রচণ্ড প্রতাপে নিজেদের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছে। কিন্তু পলাশি যুদ্ধের পর তাদের আধিপত্য ও প্রাধান্য শূন্যের কোঠায় গিরে দাঁড়ায়। ২. ইংরেজরা ক্ষমতার বসায় হিন্দুরা তাদের সমর্থন দানের প্রতিদান স্বরূপ নানা রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে নিজেদের ভাগ্যেরউন্নতি সাধন করে।
(ঘ) ইঙ্গ-ফরাসি সংঘাতের উপর প্রভাব :
(ঙ) ভারতীয় উপমহাদেশে বিজয়ের পথ প্রশস্ত:
(চ) শিক্ষার পরিবর্তন :
উপসংহার :
নিত্য নতুন সকল আপডেটের জন্য জয়েন করুন
If any objections to our content, please email us directly: helptrick24bd@gmail.com